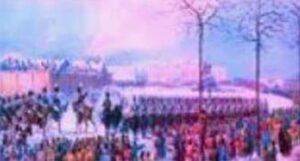ইউরোপীয় শক্তি সমবায় গঠন, উদ্দেশ্য, পবিত্র চুক্তি, চতুঃশক্তি চুক্তি, শক্তি সমবায়ের কার্যাবলী, আইলা স্যাপেলের সম্মেলন, ট্রপো সম্মেলনের পটভূমি, ট্রপো সম্মেলন, ট্রপোর ঘোষণাপত্র পাস, লাইব্যাক বৈঠক, ভ্যারোনা বৈঠক, মনরো নীতি ঘোষণা, মনরো নীতির বক্তব্য, সেন্ট পিটার্সবার্গ বৈঠক, ইংল্যান্ডের অনুপস্থিতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানবো।
ইউরোপীয় শক্তি সমবায়
| বিষয় | ইউরোপীয় শক্তি সমবায় |
| সময়কাল | ১৮১৫-১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ |
| আইলা শ্যাপেল সম্মেলন | ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ |
| ট্রপো সম্মেলন | ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ |
| লাইব্যাক সম্মেলন | ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ |
| ভ্যারোনা সম্মেলন | ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ |
| সেন্ট পিটার্সবার্গ সম্মেলন | ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ |
ভূমিকা:- ভিয়েনা সম্মেলন -এর পরবর্তীকালে ইউরোপ-এর বৃহৎ শক্তিবর্গ একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এর নাম দেওয়া হয় ‘ইউরোপীয় শক্তি সমবায়’ বা ‘কনসার্ট অফ ইউরোপ’ Concert of Europe)।
ইউরোপীয় শক্তি সমবায় গঠনের উদ্দেশ্য
‘কনসার্ট অফ ইউরোপ’ বা ইউরোপীয় শক্তি সমবায় গঠনের উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত বন্দোবস্তকে স্থায়িত্ব দান, ইউরোপে স্থায়ী শান্তি বজায় রাখা এবং ফ্রান্সকে সংযত রাখা যাতে আগামীদিনে নেপোলিয়ন -এর মতো কারো উত্থান না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা।
ফিশারের মন্তব্য
ঐতিহাসিক ফিশার বলেন যে, “ফরাসি বিপ্লব -এর ফলে ইউরোপীয় শক্তিগুলি বহু কষ্ট ভোগ করে। এজন্য ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আর কোনোভাবেই ফরাসি বিপ্লব বা নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান ঘটতে দেওয়া হবে না।”
দুটি চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপীয় শক্তি সমবায় গঠন
প্রকৃতপক্ষে দুটি চুক্তির মাধ্যমে এই ইউরোপীয় শক্তি সমবায় গড়ে ওঠে। পবিত্র চুক্তি এবং চতুঃশক্তি চুক্তি।
ইউরোপীয় শক্তি সমবায় গঠনে পবিত্র চুক্তির ভূমিকা
রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া এই চুক্তিতে প্রথম স্বাক্ষর করে। পরে একে একে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিও এতে যোগ দেয়। ইংল্যান্ড এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি।
ইউরোপীয় শক্তি সমবায় গঠনে চতুর্শক্তি চুক্তির ভূমিকা
ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া যেদিন প্যারিসের দ্বিতীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে, সেই দিনই তারা ‘চতুঃশক্তি মৈত্রী চুক্তি’ স্বাক্ষর করে (২০ শে নভেম্বর ১৮১৫ খ্রীঃ)।
ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের কার্যাবলী
১৮১৮-১৮২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চতুঃশক্তি চুক্তির চারটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনগুলি আই-লা-স্যাপেল, ট্রপো, লাইব্যাক এবং ভেরোনা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী চারটি দেশই এই সম্মেলনগুলিতে যোগদান করে।
পঞ্চম সম্মেলন
১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সম্মেলনে ইংল্যান্ড যোগদান করে নি, কারণ ততদিনে চতুঃশক্তি চুক্তি কার্যত ভেঙে গিয়েছে।
ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের আই-লা-স্যাপেল সম্মেলন (১৮১৮ খ্রিঃ)
চতুঃশক্তি চুক্তির অন্যতম শর্ত হিসেবে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানির আই-লা-স্যাপেল শহরে এই শক্তিজোটের প্রথম অধিবেশন বসে। আই-লা-স্যাপেল হল ফরাসি নাম। প্রকৃতপক্ষে এটি হল প্রাচীন জার্মান শহর আখেন (Aachen)।
(১) উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ
রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার নৃপতিবর্গ এবং মেটারনিখ, ক্যাসালরি, ওয়েলিংটন, হার্ডেনবার্গ এবং ফরাসি প্রধানমন্ত্রী রিশল্যু প্রমুখ কূটনীতিকরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।
(২) সিদ্ধান্ত
সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যেমন –
- (ক) ইতিমধ্যে ফ্রান্স তার প্রদেয় ক্ষতিপূরণের বিপুল অর্থ মিটিয়ে দিলে ফ্রান্স থেকে মিত্রশক্তির দখলদার সেনা প্রত্যাহার করা হয়। নেতৃমণ্ডলী উপলব্ধি করেন যে, ফ্রান্সের মতো একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকে শক্তি সমবায়ের বাইরে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে না। তাই পঞ্চম শক্তি হিসেবে ফ্রান্সকে এই শক্তি সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- (খ) ইতালির ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মোনাকো-র রাজার বিরুদ্ধে প্রজারা অভিযোগ জানালে তাঁকে ভর্ৎসনা করা হয়।
- (গ) ব্যাভেরিয়ার শাসনকর্তা জার্মানির রাইন অঞ্চলের ব্যাডেন নামক স্থানটি দখল করার চেষ্টা করলে ব্যাভেরিয়ার রাজাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়।
- (ঘ) সুইডেন-রাজ বার্নাদোতের বিরুদ্ধে নরওয়ে কুশাসনের অভিযোগ আনলে তাঁকে ভর্ৎসনা করা হয়।
(৩) ব্যর্থতা
বৃহৎ শক্তিগুলির পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষ সূচনা-পর্বেই প্রকট হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক কেটেলবি বলেন যে, “শক্তি সমবায়ের বাঁশির গায়ে ফুটো দেখা দেয়”এবং এর ফলে শক্তি সমবায়ের সভায় বেসুরো আওয়াজ শোনা যায়। যেমন –
- (ক) স্পেন-এর দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। স্পেন-রাজ ‘ন্যায্য অধিকার নীতি’ অনুসারে এই উপনিবেশগুলিতে নিজ কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি সমবায়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন।
- (খ) ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসালরি এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন, কারণ ইতিমধ্যে এই উপনিবেশগুলির সঙ্গে ইংল্যান্ডের লাভজনক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ইংল্যান্ডের আপত্তিতে বিষয়টি মুলতুবি থাকে, কিন্তু এর ফলে অশুভ অন্তর্বিরোধের সূচনা হয়।
- (গ) আরব জাতীয় বার্বারী জলদস্যুদের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য রাশিয়া ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রুশ নৌবহর পাঠাবার প্রস্তাব দিলে ইংল্যান্ড এই অঞ্চলে তার নিজের প্রতিপত্তি হারাবার ভয়ে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।
- (ঘ) আন্তর্জাতিক আইনে দাসব্যবস্থা নিষিদ্ধ ছিল। দাসদের চোরাচালান বন্ধের জন্য ইংল্যান্ড সমুদ্রপথে সন্দেহজনক জাহাজগুলি তল্লাশির অধিকার চাইলে, অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি আপত্তি জানায়। এইভাবে এই বৈঠকে গভীর মনোমালিন্য দেখা দেয়।
ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের ট্রপো সম্মেলনের পটভূমি
আই-লা-স্যাপেলে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে যে ফাটল ধরেছিল, ট্রপো-র বৈঠকে তা আরও বড়ো হয়ে ওঠে। যেমন –
- (১) ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে গণবিদ্রোহ দেখা দেয় এবং বুরবোঁ-বংশীয় স্পেন-রাজ সপ্তম ফার্দিনান্দ স্পেনে একটি উদারনৈতিক সংবিধান প্রবর্তনে বাধ্য হন। এতে জার প্রথম আলেকজান্ডার বিচলিত বোধ করেন এবং এই বিদ্রোহ দমনের জন্য শক্তি সমবায়কে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান।
- (২) এর উত্তরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, স্পেনের বিপ্লব সে দেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনা এবং সেক্ষেত্রে বাইরের হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনাবশ্যক। মেটারনিখ ইংল্যান্ডকে সমর্থন করেন কারণ তিনি আশঙ্কা করেন যে, এই হস্তক্ষেপে স্পেনে রুশ প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।
- (৩) কিছুদিন পর নেপলস, পিডমন্ট ও পর্তুগালে অনুরূপ উদারনৈতিক বিদ্রোহ দেখা দিলে মেটারনিখ বিচলিত হন, কারণ এর ফলে ইতালিতে অস্ট্রিয়ার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।
ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের ট্রপো সম্মেলন (১৮২০)
এই পরিস্থিতিতে ট্রপো-র বৈঠক আহুত হয় (১৮২০ খ্রিঃ)। মেটারনিখ সেখানে ট্রপো প্রোটোকল’ (Troppan Protocol) বা ট্রপো ঘোষণাপত্র’ জারি করেন। এতে বলা হয় যে,
- (১) রাজা স্বেচ্ছায় বা বিনা প্ররোচনায় যে সংবিধান প্রচলন করবেন, কেবলমাত্র সেটিই বৈধ সংবিধান বলে গণ্য হবে।
- (২) যদি ইউরোপের কোনও দেশে বিপ্লব ঘটে এবং তার ফলে সেই দেশের রাজা তাঁর বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে সেই দেশ শক্তি সমবায় থেকে বহিষ্কৃত হবে।
- (৩) যদি কোনও রাষ্ট্রে বিদ্রোহ ঘটে বা সেখানে এমন কোনও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, যার দ্বারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে শক্তি সমবায় সেনা পাঠিয়ে বলপূর্বক সেখানে শান্তি ও স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে।
আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ দমন
এই ঘোষণাপত্র দ্বারা শক্তি সমবায় ইউরোপের যে কোনও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সকলপ্রকার অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সমর্থনে সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনের হাতিয়ারে পরিণত হয়।
ইংল্যান্ডের বিরোধিতা
এই ঘোষণাপত্রের ব্যাপারে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্যাসালরি তীব্র প্রতিবাদ জানান। তার মতে এই ঘোষণা ছিল-
- (১) চতুঃশক্তি সন্ধির আদর্শ-বিরোধী।
- (২) স্পেনের বিপ্লব স্পেনের ইংল্যান্ডের প্রতিক্রিয়া অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপে সার্বভৌম দেশগুলির সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে।
- (৩) ইংল্যান্ড মনে করে যে, স্বৈরাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহের অধিকার আছে।
ট্রপোর ঘোষণাপত্র পাস
ইংল্যান্ডের আপত্তি সত্ত্বেও রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া—এই তিন প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের সমর্থনে ট্রপোর ঘোষণাপত্র পাস হয়ে যায়। ফ্রান্স এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকে। ইংল্যান্ডের সঙ্গে শক্তি সমবায়ের বিভেদ শুরু হয়।
ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের লাইব্যাক বৈঠক ( ১৮২১ খ্রিঃ)
লাইব্যাকে শক্তি সমবায়ের তৃতীয় বৈঠর বসে। এই বৈঠক অনুসারে,
- (ক) ট্রপোর ঘোষণাপত্র অনুসারে অস্ট্রিয়াকে নেপলস্-এর বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অস্ট্রিয়ার সেনাদল বুরবোঁ-বংশীয় প্রথম ফার্দিনান্দ-কে পূর্ণ ক্ষমতা-সহ নেপলস্-এর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে।
- (খ) পিডমন্ট-এ বিদ্রোহ দেখা দিলে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী তা দমন করে। এইভাবে সমগ্র ইতালি এবং ইউরোপে কিছুদিনের জন্য মেটারনিখতন্ত্র জয়যুক্ত হয়।
ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের ভেরোনা বৈঠক (১৮২২ খ্রিঃ)
১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ভেরোনা নগরীতে শক্তি সমবায়ের চতুর্থ অধিবেশন বসে। শক্তি সমবায়ের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা চিন্তা করলেও ইংল্যান্ড ডিউক অব ওয়েলিংটন-কে ভেরোনা সম্মেলনে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হয়।
ভেরোনা বৈঠকের আলোচ্য
এই সম্মেলনে দুটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল তুরস্ক-এর বিরুদ্ধে গ্রিসের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্পেনের বিদ্রোহ।
প্রতিনিধিদের মতানৈক্য
- (১) রাশিয়ার জার তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রিক খ্রিস্টানদের গ্রিস ও স্পেন সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এর ফলে বলকান অঞ্চলে রুশ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেত, যা অস্ট্রিয়া এবং ইংল্যান্ডের একেবারেই কাম্য ছিল না। এই দুই শক্তির আপত্তিতে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়।
- (২) স্পেনের প্রজা-বিদ্রোহ দমনের জন্য স্পেন-রাজ শক্তি সমবায়ের কাছে আবেদন জানান। ইংল্যান্ডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ফরাসি সেনা স্পেন ও পর্তুগালে প্রজা-বিদ্রোহ দমন করে। ক্ষুব্ধ ইংল্যান্ড শক্তি সমবায় থেকে সরে দাঁড়ায়।
- (৩) স্পেনের সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে মেটারনিখ দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ দমনে তৎপর হন। এতে ইংল্যান্ডের লাভজনক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।
ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের নির্দেশ
ইংল্যান্ড তাই বিদ্রোহী স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা মেনে নেয় এবং ব্রিটিশ নৌবহরকে আটলান্টিক মহাসাগরে শক্তি সমবায়ের জাহাজগুলি আটকাবার নির্দেশ দেয়।
মনরো নীতি ঘোষণা
এই সময় ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জেমস মনরো তাঁর সুবিখ্যাত ‘মনরো নীতি’ ঘোষণা করেন।
মনরো নীতির বক্তব্য
এই নীতিতে বলা হয় যে,
- (১) “আমেরিকা হল আমেরিকাবাসীদের জন্য।” আমেরিকায় ইউরোপীয় শক্তির হস্তক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ্য করবে না।
- (২) আমেরিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশ বিস্তারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধা দেবে।
- (৩) আমেরিকা ইউরোপের কোনও ব্যাপারে জড়াবে না।
ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের বিরত থাকা
ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার ফলে শক্তি সমবায় দক্ষিণ আমেরিকায় হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকে।
সেন্ট পিটার্সবার্গ বৈঠক (১৮২৪ খ্রিঃ)
ভেরোনা বৈঠকের পর শক্তি সমবায় কার্যত ভেঙে যায়। গ্রিসের বিদ্রোহের সমস্যা সমাধানের জন্য জার প্রথম আলেকজান্ডার সেন্ট পিটার্সবার্গে শক্তি সমবায়ের পঞ্চম সম্মেলন আহ্বান করেন।
ইংল্যান্ডের অনুপস্থিতি
ইংল্যান্ড এই সম্মেলনে যোগদান করে নি। তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে রাশিয়া গ্রিসের পক্ষ অবলম্বন করে। অস্ট্রিয়া এর বিরোধিতা করে। মেটারনিখের ধারণা হয় যে, রাশিয়া তুরস্ককে সরিয়ে গ্রিসে রুশ প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে চান।
সিদ্ধান্ত
শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, তুরস্ক এশিয় রাষ্ট্র এবং গ্রিস তুরস্কের অধীনস্থ। সুতরাং তুরস্কের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার শক্তি সমবায়ের নেই।
উপসংহার :- এরপর জার ও অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে শক্তি সমবায়ের পতন ঘটে।
(FAQ) ইউরোপীয় শক্তি সমবায় সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য?
পাঁচটি।
১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে আই-লা-শ্যাপেল শহরে।
১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে।
১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে।