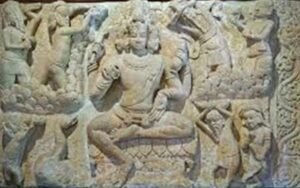ঋকবৈদিক যুগের রাজনৈতিক জীবন প্রসঙ্গে উপজাতি, পরিবার, যুদ্ধবিগ্ৰহ, দশ রাজার যুদ্ধ, যুদ্ধের কাহিনী থেকে প্রাপ্ত তথ্য, রাজপদের উদ্ভব, রাজার কর্তব্য, রাষ্ট্রের স্তরবিন্যাস, কর্মচারী শ্রেণী, দুটি সংস্থা সভা ও সমিতি সম্পর্কে জানবো।
আর্যদের ঋকবৈদিক যুগের রাজনৈতিক জীবন
| ঐতিহাসিক ঘটনা | ঋকবৈদিক যুগের রাজনৈতিক জীবন |
| রাষ্ট্রের ব্যবস্থা | উপজাতি কেন্দ্রিক |
| উপাদান | ঋগ্বেদ |
| সংস্থা | সভা ও সমিতি |
| কর | বলি |
ভূমিকা :- বৈদিক যুগকে পণ্ডিতেরা সাধারণত দুভাগে ভাগ করেন – ঋক বৈদিক যুগ ও পরবর্তী বৈদিক যুগ। ঋকবেদের যুগের সঙ্গে পরবর্তী বৈদিক যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়।
ঋকবৈদিক যুগের রাজনীতি সম্পর্কে উপাদান
- (১) ঋকবৈদিক যুগের সভ্যতা সম্পর্কে ঋকবেদ হল প্রধান উপাদান। ঋকবেদের স্তোত্রগুলি দীর্ঘকাল ধরে রচিত হয়। আনুমানিক ১৫০০ বা ১৪০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত ঋকবেদের রচনাকাল ছিল।
- (২) হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্রে খনন করে ঋকবেদের যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। যদিও অনেকে এই প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ঋকবৈদিক আর্যদের সভ্যতার নিদর্শন নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন।
ঋকবৈদিক যুগের উপজাতি
প্রাচীন ঋকবেদের যুগে আর্যদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল প্রধানতঃ উপজাতি কেন্দ্রিক। পরবর্তী বৈদিক যুগের ন্যায় বৃহৎ ভৌগোলিক রাষ্ট্র ঋকবেদের যুগে গড়ে উঠে নি। ঋকবেদের যুগে আর্যরা ভরত, যদু, সঞ্জয়, অনু, পুরু, তুর্বস প্রভৃতি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল।
ঋকবৈদিক যুগে পরিবার
প্রাচীন ঋকবেদের যুগে পরিবার ছিল রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন স্তর। পিতা-মাতা, পিতামহ ও পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়দের নিয়ে পরিবার গঠিত হয়। রক্ত সম্পর্ক দ্বারা পরিবারের বন্ধন স্থির করা হত। পরিবারের প্রধান বা কুলপতি বা কুলপা ছিল পরিবারের শাসনকর্তা। কতকগুলি পরিবার রক্ত সম্পর্কে যুক্ত হলে গোষ্ঠী বা উপজাতি গঠিত হত।
ঋকবৈদিক যুগে যুদ্ধবিগ্ৰহ
প্রাচীন ঋকবেদের যুগে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত। এই যুদ্ধের কারণ ছিল কৃষি ও পশুচারণ ভূমির অধিকার নিয়ে বিবাদ। ভারত -এর আদিবাসী অনার্য বা দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্যগোষ্ঠীগুলির যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত। ঋকবেদে দশ রাজার যুদ্ধের উপাখ্যান একথা প্রমাণ করে যে, আর্য উপজাতিগুলি আদপেই শান্তিপ্রিয় ছিল না।
ঋকবৈদিক যুগে দশ রাজার যুদ্ধ
- (১) দশ রাজার যুদ্ধ -এর কাহিনী থেকে জানা যায় যে, রাজা নিবোদাসের পুত্র রাজা সুদাস ছিলেন ভরত বা ভারত গোষ্ঠীর রাজা। তার রাজ্য ছিল পশ্চিম পাঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চলে। তার পুরোহিত ছিলেন বিশ্বামিত্র। কিন্তু সুদাস এই পুরোহিতের কাজে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তাঁর স্থলে বশিষ্ঠকে প্রধান পুরোহিত রূপে নিয়োগ করেন।
- (২) এই কারণে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে দশটি আর্য উপজাতির দশ রাজার জোট গড়ে সুদাসকে আক্রমণ করেন। বহু বাধা-বিপত্তির পর সুদাস জয়লাভ করেন। আর্যদের গোষ্ঠী যুদ্ধে অনার্যরাও অংশ নিত। এইভাবে আর্য সভ্যতার সঙ্গে অনার্য বা দ্রাবিড় সভ্যতার মিশ্রণ আরম্ভ হয়।
ঋকবৈদিক যুগে দশ রাজার যুদ্ধের কাহিনী থেকে প্রাপ্ত তথ্য
দশ রাজার যুদ্ধের কাহিনী থেকে যে তথ্যগুলি পাওয়া যায় তা হল –
- (১) ঋকবেদের যুগে গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকত। এর ফলে তাদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠীগুলিকে জয় করে একরাট হওয়ার প্রবণতা এই সময় দেখা দেয়।
- (২) রাষ্ট্রের শাসনে পুরোহিতের স্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরোহিত ছিল একাধারে মন্ত্রী, কূটনীতিবিদ এবং রাজার ডান-হাত।
- (৩) দশ রাজার যুদ্ধে ভরত গোষ্ঠীর জয়লাভ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গোষ্ঠী আর্য সভ্যতার প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়। ভরত উপজাতির নামে এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়।
- (৪) ডি. ডি. কোশাম্বীর মতে, ভরত গোষ্ঠীর রাজা দিবোদাস ও সুদাসের নামের শেষে দাস পদবীটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। কোশাম্বীর মতে, দাস শব্দটি থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, ভরত গোষ্ঠীতে আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণ ঘটেছিল।
- (৫) পরবর্তীকালে দাস শব্দটি যেরূপ ঘৃণাজনক অর্থে ব্যবহার করা হত এই যুগে তা হত না। ভরত গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী দশ রাজার গোষ্ঠী খাঁটি আর্যদের জোট ছিল এমন কথা বলা যায় না।
ঋকবৈদিক যুগে রাজপদের উদ্ভব
- (১) নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য এবং গোষ্ঠীদের উপজাতির মধ্যে শৃঙ্খলা রাখার জন্যে রাজ পদের উদ্ভব হয়। রোমিলা থাপারের মতে, ঋকবেদের যুগের রাজারা ছিল প্রধানত যোদ্ধাদের নেতা।
- (২) ঋকবেদে রাজতন্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধের সময় জয়ের জন্য দেবতারা তাদের রাজা নির্বাচন করেন বলে একটি কাহিনী পাওয়া যায়। এই কাহিনী থেকে রাজতন্ত্রের উদ্ভব এবং নির্বাচন দ্বারা রাজা নিয়োগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
- (৩) ঋকবেদের দশম স্তোত্রে অনেক আর্য রাজার নাম পাওয়া যায়। এই রাজারা এক একটি আর্য উপজাতির ওপর রাজত্ব করতেন। কার্যতঃ রাজা বংশানুক্রমিকভাবেই ক্ষমতা ভোগ করতেন। ক্রমে ক্রমে রাজা নিজেকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করেন।
- (৪) অভিষেক প্রথার দ্বারা রাজাকে সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বর্গীয় অধিকার যুক্ত বলে ঘোষণা করা হত। পুরোহিত রাজার অভিষেক করতেন। এভাবে রাজা ও রাজপুরোহিত একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা ও সম্মান অধিকার করেন। ঋকবেদের রাজাকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলা হলেও, তাঁর সার্বভৌম অধিকার রক্ষার জন্য জনসমর্থন লাভের কথাও বলা হয়েছে।
ঋকবৈদিক যুগে নির্বাচন ও প্রজাতন্ত্র
ঋকবেদের যুগে রাজপদ বংশানুক্রমিক হলেও নির্বাচিত রাজতন্ত্রের কথা জানা যায়। বিশ বা গোষ্ঠী দরকার হলে রাজাকে নির্বাচন করত। ঋকবেদের যুগে প্রজাতন্ত্রও ছিল বলে জানা যায়। কতকগুলি গোষ্ঠী বা উপজাতি তাদের শাসনকর্তা নির্বাচন করত। গোষ্ঠী প্রধানরা নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র শাসন করত। এই শাসন ব্যবস্থা খাঁটি প্রজাতন্ত্র না হলেও নির্বাচিত অভিজাততন্ত্র ছিল একথা বলা যায়।
ঋকবৈদিক যুগে রাজার কর্তব্য
- (১) ঋকবেদের যুগে রাজার প্রধান কাজ ছিল শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা, প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। লুডউইগের মতে, পুরোহিতের সাহায্যে রাজাকে প্রজাদের আবেদনের ন্যায় বিচার করতে হত। দোষীকে শাস্তি দিতে হত।
- (২) ঋকবেদের যুগে গোধন অপহরণ, বলপূর্বক জমি ও সম্পত্তি দখল করার খুব চেষ্টা হত। রাজাকে এই সকল অন্যায়ের প্রতিকার করতে হত। রাজা সমাজে সম্মান ও প্রতিপত্তি ভোগ করতেন।
- (৩) ঋকবেদের যুগে রাজারা প্রজাদের কাছ থেকে কোনো নিয়মিত কর পেতেন না। রাজা ‘বলি’ নামক এক প্রকার অনিয়মিত কর পেতেন। আবার ‘বলি’ কথাটির অর্থ যজ্ঞে বলি দেওয়া পশুর ভাগ বুঝায়। সুতরাং রাজা নিয়মিত কোনো কর পেতেন না। একথা বলা যায় জনসাধারণ স্বেচ্ছায় কর দিত।
- (৪) জমির ওপর রাজার কোনো স্বত্ব নেই বলে উল্লেখ দেখা যায়। রাজা অর্থ, তৈজসপত্র দান করলেও ভূমি দান করতেন না। কারণ, ভূমির মালিক তিনি ছিলেন না। যুদ্ধে জয় হলে শত্রুর সম্পত্তি লুঠ করে যা পাওয়া যেত এবং অন্য আর্য গোষ্ঠীর পশু লুঠ করা হলে রাজা তার ভাগ পেতেন।
ঋকবৈদিক যুগে রাষ্ট্রের স্তর বিন্যাস
রাজ্যকে শাসন করার জন্য এই যুগে রাষ্ট্রকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হত। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গোষ্ঠী বা Tribe গঠিত হত। কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে গ্রাম এবং কয়েকটি গ্রাম নিয়ে বিশ বা জন গঠিত হত এবং কয়েকটি জন নিয়ে দেশ বা রাষ্ট্র গঠিত হত। গ্রামনী গ্রামের শাসন করত। বিশপতি বিশ-এর এবং গোপ জন-এর শাসন করত। তবে বিশ ও জনের সম্পর্ক সঠিক কি ছিল তা জানা যায় নি।
ঋকবৈদিক যুগে কর্মচারী শ্রেণী
- (১) রাজাকে শাসন কাজে সাহায্যের জন্যে বিভিন্ন কর্মচারী নিযুক্ত হত। কুলের অধিপতি ছিল কুলপা বা কুলপতি। পুরোহিত রাজার খুবই ঘনিষ্ঠ কর্মচারী ছিলেন। যাগযজ্ঞ ও ধর্মীয় ব্যাপারে পুরোহিত ছিলেন সর্বেসর্বা। রাজাকে রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক পরামর্শদান করা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রেও পুরোহিত রাজার সঙ্গে যেতেন।
- (২) সেনানী নামক কর্মচারী সেনাদল গঠন ও যুদ্ধ-বিগ্রহের দায়িত্ব পালন। করত। গ্রামনী গ্রামের সামরিক ও অসামরিক কাজের দায়িত্ব বহন করত। দূত ও গুপ্তচর শত্রুর গতিবিধির খবর আনত। দূত কূটনৈতিক কাজও করত।
ঋকবৈদিক যুগে সেনাবাহিনী ও অস্ত্র
ঋকবেদের যুগে পদাতিক ও রথারোহী সেনা ছিল। তীর, ধনুক, বল্লম, তলোয়ার, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করা হত। ‘রথমুষল’ নামে এক প্রকার অস্ত্র ছিল। ছুটন্ত রথ হতে এই যন্ত্রের দ্বারা অস্ত্র নিক্ষেপ করা হত। ঋকবেদে পুরচরিষ্ণু বা ছুটন্ত দুর্গের কথা বলা হয়েছে যা থেকে তীর ছোড়া হত এবং রথমুষলও ছোড়া হত। মনে হয় ছুটন্ত রথকেই ‘পুরচরিষ্ণু’ বলা হয়েছে।
ঋকবৈদিক যুগে সভা ও সমিতি
সভা ও সমিতি নামে ঋকবেদের যুগে দুটি সংস্থা ছিল। কিন্তু এই দুটি সংস্থার গঠন ও ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি। বৈদিক সাহিত্যের পণ্ডিতেরা সভা ও সমিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মতামত প্রকাশ করেন। যেমন –
(১) লুড উইগের মতে, সভা ছিল উপজাতির প্রধানদের নির্বাচিত পরিষদ এবং সমিতি ছিল উপজাতির সর্বসাধারণের পরিষদ। আবার কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে, সভা ছিল গ্রাম পরিষদ এবং সমিতি ছিল জন পরিষদ। সমিতির ক্ষমতা সভা অপেক্ষা বেশী ছিল একথা মনে করা যায়।
ঋকবৈদিক যুগে সমিতি
- (১) সমিতির অধিবেশনে রাজা, অভিজাত বা প্রধান ব্যক্তিরা ও জনসাধারণ একত্র মিলিত হতেন। সমিতি রাজার কর্তব্যের নির্দেশ দিতে পারত। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিঃসন্দেহে সমিতির ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল। এই রাষ্ট্রে সমিতিই ছিল শাসন ব্যবস্থার মূল কেন্দ্র। এরূপ প্রজাতন্ত্রের সংখ্যা বৈদিক যুগে খুব কম ছিল না।
- (২) রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও সমিতির ক্ষমতা ঋকবেদের যুগে কম ছিল না। রাজা সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থেকে তাঁর বক্তব্যের দ্বারা সমিতির সদস্যদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন।
- (৩) ঋকবেদে জনসাধারণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমিতির অধিবেশনে তারা যেন ঐক্যবদ্ধ থাকে, একই মতে কথা বলে, একই মন, একই চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করে। অর্থাৎ সংগচ্ছধ্বম, সংবদদ্ধম, সহমনম, সহবিত্তম, সমান মন্ত্রম হয়। জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হলে রাজার পক্ষে স্বৈরাচারী হওয়া সম্ভব হবে না এই ছিল এই মন্ত্রের মূল কথা।
- (৪) এই মন্ত্রের মধ্যে আমরা ফ্রান্স -এর দার্শনিক রুশোর জেনারেল উইল বা সর্বসাধারণের সম্মতি তত্ত্বের আভাষ পাই। যতদিন রাষ্ট্র উপজাতি-কেন্দ্রিক ছিল ততদিন সমিতির ক্ষমতা বেশী ছিল। পরে রাষ্ট্রের আয়তন বাড়লে সমিতির ক্ষমতা কমে যায়।
ঋকবৈদিক যুগে সভা
সভা সম্পর্কে বলা যায় যে, সভা বয়স্ক, প্রধান ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান ছিল। ঋকবেদের যুগে সভার ক্ষমতা কি ছিল তা সঠিক জানা যায় নি। তবে পরবর্তী বৈদিক যুগে সভার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
উপসংহার :- প্রাচীন গ্রিস -এ যে পলিস ব্যবস্থা ছিল, বৈদিক আর্যদের উপজাতিক রাষ্ট্র ছিল অনেকটা পলিসের মতই। তবে ঋকবৈদিক যুগের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল উপজাতি কেন্দ্রিক।
(FAQ) ঋকবৈদিক যুগের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য?
সভা ও সমিতি।
উপজাতি কেন্দ্রিক।
ঋকবৈদিক যুগের এক প্রকার অনিয়মিত কর।
দশ রাজার যুদ্ধ।