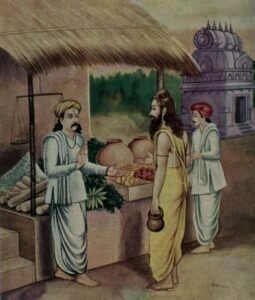আজ পরবর্তী বৈদিক যুগ কাকে বলে? পরবর্তী বৈদিক যুগের সাহিত্য, রাজনৈতিক অবস্থা, রাজস্ব আদায়, বিচারব্যবস্থা, সামাজিক জীবন, বর্ণপ্রথা, নারীর মর্যাদা, খাদ্য, পোশাক, অর্থনৈতিক জীবন, ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে জানবো।
ইতিহাসে পরবর্তী বৈদিক যুগ প্রসঙ্গে পরবর্তী বৈদিক যুগ কাকে বলে, পরবর্তী বৈদিক যুগের সময়কাল, পরবর্তী বৈদিক যুগের সাহিত্য, পরবর্তী বৈদিক যুগের রাজনৈতিক অবস্থা, পরবর্তী বৈদিক যুগের বৃহৎ সাম্রাজ্য, পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজার ক্ষমতা, পরবর্তী বৈদিক যুগে সভা সমিতির গুরুত্ব হ্রাস, পরবর্তী বৈদিক যুগের রাজস্ব আদায়, পরবর্তী বৈদিক যুগের বিচার ব্যবস্থা, পরবর্তী বৈদিক যুগের সমাজ জীবন, পরবর্তী বৈদিক যুগে বর্ণপ্রথা, পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর মর্যাদা, পরবর্তী বৈদিক যুগে মানুষের খাদ্য, পরবর্তী বৈদিক যুগে মানুষের পোশাক, পরবর্তী বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক জীবন, পরবর্তী বৈদিক যুগের কৃষি, পশুপালন, ব্যবসা বাণিজ্য ও পরবর্তী বৈদিক যুগের ধর্মীয় জীবন।
পরবর্তী বৈদিক যুগ
| বিষয় | পরবর্তী বৈদিক যুগ |
| ভিত্তি | সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য |
| সময়কাল | ১০০০-৬০০ খ্রিষ্টপূর্ব |
| সমাজ | পিতৃতান্ত্রিক |
| বিদুষী নারী | গার্গী ও মৈত্রেয়ী |
ভূমিকা :- বৈদিক সভ্যতার শেষ ভাগ হল পরবর্তী বৈদিক যুগ। প্রথম পর্ব ঋক বৈদিক যুগ -এর বিভিন্ন অবস্থা পরবর্তী বৈদিক যুগে পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়।
পরবর্তী বৈদিক যুগ
আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কালকে পরবর্তী বৈদিক যুগ বলা হয়।
পরবর্তী বৈদিক যুগের সাহিত্য
এই যুগে সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদ এবং অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়।
পরবর্তী বৈদিক যুগের রাজনৈতিক অবস্থা
পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।
(১) পরবর্তী বৈদিক যুগে বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন
- (ক) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজাদের সম্রাট, বিরাট, স্বরাট, একরাট, সার্বভৌম প্রভৃতি রাজকীয় অভিধা গ্রহণের উল্লেখ আছে।
- (খ) রাজারা নিজেদের ওইসব অভিধার যোগ্য প্রতিপন্ন করার জন্য অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞের আয়োজন করতেন।
- (গ) শতপথ ব্রাহ্মণে কোশল রাজ এবং মৎস্য রাজ কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের উল্লেখ আছে। এই সব থেকে এই যুগে বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
(২) পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজার ক্ষমতা
- (ক) পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজার ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর ওপর দৈবস্বত্ব আরোপিত হয়। রাজাকে প্রজাপতি বা ব্রহ্মার প্রতিনিধি মনে করা হত।
- (খ) রাজা ছিলেন অভ্রান্ত ও সকল শাস্তির ঊর্ধ্বে। ব্রাহ্মণ ছাড়া সবার উপর রাজার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- (গ) ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি থেকে এই যুগের রাজাদের সম্রাট, বিরাট, স্বরাট, একরাট প্রভৃতি অভিধা গ্রহণ এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ইঙ্গিত রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার পরিচয় বহন করে।
(৩) পরবর্তী বৈদিক যুগে সভা ও সমিতির গুরুত্ব হ্রাস
রাজার স্বৈরক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে পরবর্তী বৈদিক যুগে সভা ও সমিতির গুরুত্ব হ্রাস পায়।
(৪) পরবর্তী বৈদিক যুগের রাজকর্মচারীবৃন্দ
- (ক) রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসনকার্যে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। ঋক বৈদিক যুগের গ্রামণী, সেনানী ও পুরোহিত শ্রেণী এই যুগেও রাজকার্যে নিযুক্ত ছিল।
- (খ) এই যুগে ভাগদূত বা কর আদায়কারী, সংগ্রহিত্রী বা কোষাধ্যক্ষ, সূত বা রাজকীয় ঘোষক (রথ চালক), ক্ষত্রী বা রাজসংসারের সরকার, অক্ষবাপ বা জুয়াখেলার অধ্যক্ষ, গোবিকর্তন বা রাজার শিকারসঙ্গী, পালাগল বা রাজার সংবাদবাহক প্রভৃতি নতুন রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়।
(৫) পরবর্তী বৈদিক যুগের প্রাদেশিক শাসন
এই সময় প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সূচনা হয়। প্রাদেশিক শাসনকার্যের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে ছিলেন –
- (ক) স্থপতি – সীমান্ত অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।
- (খ) শতপতি – একশোটি গ্রামের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।
- (গ) গ্রামণী – গ্রামের শাসক।
- (ঘ) অধিকৃত – গ্রাম্য স্তরের সরকারি কর্মচারী।
- (ঙ) উগ্র – গ্রামের শাস্তিরক্ষক।
পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজস্ব আদায়
- (১) এই যুগে প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য নিয়মিত কর আদায়ের ব্যবস্থা চালু হয়।
- (২) রাজস্ব আদায়ের জন্য সংগ্রহিত্রী ও ভাগদূত নামে দুজন কর্মচারী নিযুক্ত হয়।
- (৩) বলি ও শুল্ক নামে দুধরনের রাজস্ব এই সময় আদায় করা হত।
- (৪) ঋক বৈদিক যুগে বলি ছিল ঐচ্ছিক কিন্তু এই যুগে বলি প্রদান বাধ্যতামূলক হয়।
- (৫) ব্রাহ্মণ ও রাজপরিবারের সদস্যদের কোনও রাজস্ব দিতে হত না, জনসাধারণই তা বহন করত।
পরবর্তী বৈদিক যুগের বিচারব্যবস্থা
- (১) বিচার ব্যবস্থায় রাজাই ছিলেন সর্বেসর্বা। অবশ্য তিনি সর্বদা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন না। বিচারের দায়িত্ব ছিল অধ্যক্ষর উপর।
- (২) গ্রামের ছোটোখাটো বিচার করত গ্রাম্যবিচারক বা গ্রাম্যবাদীন। দেওয়ানি মামলা সাধারণত সালিশির মাধ্যমে মেটানো হত। এই যুগে অপরাধীকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হত।
পরবর্তী বৈদিক যুগে সামাজিক জীবন
ঋক বৈদিক যুগের মতো এই যুগেও পরিবার ছিল সমাজব্যবস্থার ভিত্তি এবং বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই ছিলেন পরিবারের কর্তা।
পরবর্তী বৈদিক যুগে বর্ণপ্রথা
- (১) পরবর্তী বৈদিক যুগে চারটি বর্ণ ছাড়াও নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণের উৎপত্তি হয়।
- (২) ছুতোর, কর্মকার, চর্মশিল্পী, মৎস্যজীবী প্রভৃতি পেশার মানুষরা কর্মভিত্তিক ও বংশানুক্রমিক বর্ণ বা জাতি গড়ে তোলে। ফলে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়।
- (৩) সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বাড়ে। শূদ্ররা সমাজের উচ্চ তিন বর্ণের নিপীড়নের শিকার হয়। সমাজে অস্পৃশ্যতা বৃদ্ধি পায়।
পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর মর্যাদা
পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর মর্যাদা বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়।
- (১) তাঁরা আর আগের মতো উপনয়নের এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কাজে যোগদানের অধিকারী ছিলেন না।
- (২) সমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, নারীর বহুপতিত্ব, পণপ্রথা প্রভৃতি প্রচলিত হয়।
- (৩) কন্যাসন্তান অনভিপ্রেত ছিল। নারীকে পণ্য ও ভোগের সামগ্রী বলে মনে করা হত। তা সত্ত্বেও এই যুগের কৃতি মহিলাদের মধ্যে গার্গী ও মৈত্রেয়ী উল্লেখযোগ্য ছিলেন।
পরবর্তী বৈদিক যুগে মানুষের খাদ্য
এই যুগে যবের সঙ্গে বৃহি বা ধান প্রধান খাদ্যরূপে স্বীকৃত হয়। এছাড়া গোধুন বা গম, দুধ ও মাংসাহার ছিল সাধারণ ও ব্যাপক। গো হত্যা নিন্দনীয় হতে থাকে।
পরবর্তী বৈদিক যুগের পোশাক
- (১) পরবর্তী বৈদিক যুগের পুরুষ ও মহিলারা সুতি, পশম ও পশুচর্ম ছাড়াও রেশম ও ছাগলের লোম পরিধেয় হিসাবে ব্যবহার করত। রঙিন ও মূল্যবান পোশাকও লোকে পছন্দ করত।
- (২) নারী-পুরুষ উভয়েই সোনা ও মূল্যবান পাথরের অলংকার পরত চামড়ার তৈরি চটি ও জুতো ব্যবহারের কথা জানা যায়।
- (৩) এছাড়া চিরুনি বা শলালি, ধাতুনির্মিত আয়না বা প্রকাশ ও শঙ্খ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত।
পরবর্তী বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক জীবন
পরবর্তী বৈদিক যুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনগুলি হল –
(১) পরবর্তী বৈদিক যুগের কৃষি
কৃষি ছিল প্রধান জীবিকা। এই যুগে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।
- (ক) ধান, গম, যব, তুলো, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি প্রভৃতি ছিল প্রধান শস্য।
- (খ) এই যুগে কৃষিক্ষেত্রে লৌহ উপকরণের ব্যবহার, জমিতে সারের ব্যবহার, চব্বিশটি বলদে টানা লাঙলের উল্লেখ আছে।
- (গ) জমির মালিকানা ছিল পরিবারের হাতে এবং তা উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করা যেত। সাধারণভাবে জমির মালিক নিজে চাষ করত।
- (ঘ) এই যুগে বেশি জমির মালিক এক অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যারা অন্যকে দিয়ে চাষ করিয়ে শুধু রাজস্ব ভোগ করত।
(২) পরবর্তী বৈদিক যুগে পশুপালন
গৃহপালিত পশুর মধ্যে প্রধান ছিল গোরু। কৃষির প্রয়োজনে গোহত্যা বন্ধ হয়। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে গোহত্যা প্রচলিত ছিল। গোরু ছাড়াও ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, মহিষ প্রভৃতি ছিল গৃহপালিত পশু। যুদ্ধের প্রয়োজনে হাতি ব্যবহার করা হত।
(৩) পরবর্তী বৈদিক যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য
এই যুগ ছিল বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের যুগ। এই যুগে অভ্যন্তরীণ ছাড়াও বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।
- (ক)পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে শ্রেষ্ঠিন বা ধনী ব্যবসায়ীর কথা বলা হয়েছে। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ব্যবসায়ীরা সংঘবদ্ধভাবে নিগম বা গিল্ড গড়ে তোলে।
- (খ) বস্ত্র, ছাগলের চামড়া প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় হত। কিরাত নামে এক পার্বত্য উপজাতি মৃগনাভি ও বিভিন্ন ভেষজের বিনিময়ে বস্ত্র ও চামড়া সংগ্রহ করত।
- (গ) তাঁতি, মৃৎশিল্পী ও স্বর্ণশিল্পীর সঙ্গে যুক্ত হয় জুহুরী, রঞ্জনশিল্পী, ধোপা, পাচক, চিকিৎসক, গণৎকার, নৃত্যশিল্পী, বংশীবাদক, রথচালক, সুদের কারবারী প্রভৃতি নতুন পেশার মানুষ।
(৪) পরবর্তী বৈদিক যুগে ধাতুর ব্যবহার
ধাতুর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সোনা, রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জের সঙ্গে এই যুগে যুক্ত হয় সীসা, টিন ও লোহা। লোহার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে নতুন অঞ্চলে বসতি স্থাপন ও কৃষির অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল।
(৫) পরবর্তী বৈদিক যুগের ধাতব মুদ্রা
ধাতব মুদ্রার প্রচলন ছিল কি না তা জানা যায় না। তবে জানা যায় যে মান ছিল ওজনের একক এবং একটি মানের সমতুল্য ছিল এক কৃষ্ণল। একশোটি কৃষ্ণল ছিল একটি স্বর্ণখণ্ডের সমান, যার নাম শতমান। পূর্ববর্তী যুগের নিস্ক এই যুগেও প্রচলিত ছিল।
পরবর্তী বৈদিক যুগের ধর্মীয় জীবন
- (১) পরবর্তী বৈদিক যুগের ধর্মীয় জীবনে যাগযজ্ঞ ও জটিল আচার অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- (২) ইন্দ্র ও অগ্নির মতো ঋক বৈদিক দেবতারা মর্যাদা হারান পরবর্তী বৈদিক যুগে। জীবজগতের স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন।
- (৩) এই যুগে রুদ্রদেবের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে তিনি শিবে রূপান্তরিত হন। বিষ্ণুর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের প্রধান রক্ষাকর্তা হিসাবে পরিগণিত হন।
- (৪) এযুগের শেষের দিকে কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ নামে নতুন দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে।
উপসংহার :- বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত নামে দুটি মহাকাব্য রচনা করেন। এই সময়কালকে মহাকাব্যের যুগ বলা হয়।
প্রিয় পাঠক/পাঠিকা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় করে আমাদের এই “পরবর্তী বৈদিক যুগ” পোস্টটি পড়ার জন্য। এই ভাবেই adhunikitihas.com ওয়েবসাইটের পাশে থাকুন। যেকোনো প্রশ্ন উত্তর জানতে এই ওয়েবসাইট টি ফলো করুণ এবং নিজেকে তথ্য সমৃদ্ধ করে তুলুন।
সবশেষে আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ যদি এই পোস্টটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে Comment ও Share করে দিবেন, (ধন্যবাদ)।
(FAQ) পরবর্তী বৈদিক যুগ হতে জিজ্ঞাস্য?
গার্গী ও মৈত্রেয়ী।
প্রজাপতি ব্রহ্মা।
১০০০-৬০০ খ্রিষ্টপূর্ব।